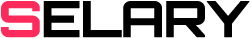আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। ছোটসময় থেকেই বামপন্থীদের দেখে বড় হওয়া। বাড়িতে ছিল বামপন্থীদের আনাগোনা। কিন্তু আমার তেমনটা আগ্রহ ছিল না, কোনো কিছু আগবাড়িয়ে জানার। অনেকেই আমাদের বাড়িতে আসতেন। কিন্তু প্রতিনিয়ত ‘কৃষক মুক্তি সংগ্রাম’ এর একজন নেতা আসতেন। পড়াশুনার খোঁজ-খবর নিতেন, পাঠ্য বইয়ের বাইরে কোনো বই পড়ি কিনা- প্রশ্ন করতেন। সেদিন রাত আটটা। পড়ার টেবিলে গুনগুন করে পড়ছি। তিনি আসলেন- তার হাতে মহাশ্বেতা দেবীর ‘হাজার চুরাশির মা’। বইটি হাতে নিলাম, উৎসাহ প্রকাশ করলাম। পড়ার জন্য ধার নিবো ভাবছি। তিনি বললেন, বইটি তোমার জন্যই এনেছি। পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি বইটি পড়া শুরু করলাম। মাঝেমধ্যেই আটকে যাই, বুঝতে পারি না। কী সব চরিত্র! ইমদাদুল হক মিলন, হুমায়ুন আহমেদ-ই তো ভালো-মনে মনে ভাবি। এই বইগুলো স্কুলের লাইব্রেরিতে পড়ার সুযোগ হয়েছে। বেশ কয়েক দিনে বইটি শেষ করলাম, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি নি। আবার পড়তে বলা হলো, আবারও পড়লাম। কিছুটা বুঝলাম। কিছুটা বুঝানো হলো। পার্টিতে পেশাদার জীবন-যাপন করার সময় বইটি আরো দু’বার পড়ি, এখনও মাঝেমধ্যেই পৃষ্ঠা ওল্টাই। আরো পরিষ্কারভাবে বুঝি এবং বইটি আমাকে নাড়া দেয়। নকশালবাড়ি আন্দোলন নিয়ে উপন্যাসটি লেখা। বাঙালি শহরে মধ্যবিত্ত জীবনের ঠুনকো মূল্যবোধ; ভেঙে দিয়ে এক নারীর উচ্চতায় তুলে আনা। তাছাড়াও এই বইটিতে মূলত তিনি তাঁর ছেলে নবারুণের চরিত্রটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এই উপন্যাসটিতে বিপ্লবের জয়ধ্বনি শুনতে পাই। যেমন শুনতে পাই- মাক্সিম গোর্কির ‘মা’, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পথের দাবি’, গ্রামে চলো, বিপ্লবের গান, 'কী করে ভালো কমিউনিস্ট হওয়া যায়’ বইগুলো পড়ে। ‘হাজার চুরাশির মা’ বইয়ে ব্রতীর শৈশবচিত্রটা বাস্তবতার নিরিখে আঁকা। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ব্রতীর চরিত্রটা তাঁরই ছেলে নবারুণের শৈশবের চিত্র। নবারুণের ডাক নাম ছিল- বাপ্পা। মহাশ্বেতা দেবী আদর করে ‘বাবু’ বলে ডাকতেন। ছেলের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একটা সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন- "বাপ্পা বই পাগল ছিল। বই পড়তে ভীষণ ভালোবাসতেন। ওর মতো ছেলের নিজস্ব একটা জগত থাকবেই। সেই জগতেই ও থাকত। ও একেবারেই বইয়ের জঙ্গলের মধ্যে শিকারী হয়ে ঘুরে বেড়াতো। বাপ্পা শুরুই করেছিল কবিতা দিয়ে। ওর একটা কবিতা খুব মনে পড়ে, ‘একটা কথার ফুলকি উড়ে শুকনো ঘাসে পড়বে কবে/ সারা শহর উত্থাল-পাথাল, ভীষণ রাগে যুদ্ধ হবে/ফাটবে চিবুক, পোড় খাবে বুক, একটা নদী উতল হয়ে’। কিছু দিন পর ও খুব মন দিয়ে গল্প লিখতে শুরু করল। বই পড়ার পাশাপাশি ও খেতেও খুব ভালোবাসতো। মাংসের একটা রান্না আমি করতাম, পুরনো দিনের, রেজালা, সেটা ছিল ওর খুব পছন্দের। ও সিনেমা দেখতে খুব ভালোবাসত"। বাপ্পা তাঁর জীবন থেকে সরে গিয়েছিল। জীবন ও পরিবার নিয়ে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। সেই জীবনের আলোকেই ‘হাজার চুরাশির মা’ উপন্যাসটি লিখেছিলেন তিনি। তখন থেকেই এই মানুষটিকে জানার এবং বোঝার তীব্র আগ্রহ। কিন্তু যে মানুষটি আমাকে ‘হাজার চুরাশির মা’ বইটি দিয়েছিলেন তিনিও খুব বেশি জানেন না- মহাশ্বেতা দেবী সম্পর্কে। তাঁর সাহিত্য যতই পড়ছি ততই সমৃদ্ধ হচ্ছি। মানুষটি নারী আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ, গণমানুষের আন্দোলন নিয়ে লিখেছেন। যার জীবনদর্শনই ছিল- লেখনী। সেই মানুষটিকে এই লেখায় তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রয়াসমাত্র। মহাশ্বেতা দেবী। একজন লড়াকুর নাম। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, নারী আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ ও মানবাধিকার কর্মী ছিলেন। যিনি লেখনীর মধ্যদিয়ে জাগিয়ে তুলেছেন হাজারো ছাত্র-তরুণকে। যতদিন মানবসভ্যতা টিকে থাকবে ততদিন তাঁর লেখনী লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে। তিনি ঢাকারই মানুষ ছিলেন। ১৯২৬ সালের ১৪ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর বাবা মণীশ ঘটক। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক। তাঁর কাকা বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ঋত্বিক ঘটক। যিনি সিনেমার মধ্যদিয়ে সমাজের অন্যায়, অবিচার, বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেছিলেন সুনিপুণভাবে। মহাশ্বেতা দেবী মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পড়াশুনার হাতেখড়ি মা-বাবার হাত ধরেই। বাবার চাকরির কারণে বাংলাদেশে পড়াশুনা করার সুযোগ হয় নি তাঁর। মহাশ্বেতা দেবী শিক্ষালাভের জন্য শান্তিনিকেতনে ভর্তি হন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬২ সালে বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। সংসার ভেঙে গেলে ছেলের জন্য খুব কষ্ট পেয়েছিলেন তিনি। সেসময় তিনি অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করতেও গিয়েছিলেন, চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টায় বেঁচে যান। এরপর তিনি অসিত গুপ্তকে বিয়ে করেন ১৯৬৫ সালে, সে সংসারও টিকেনি, ১৯৭৬ সালে ভেঙে যায়। নিঃসঙ্গ জীবন, বিচ্ছেদ-বিরহ-বেদনায় তিনি নিজেকে সঁপে দেন লেখা এবং শিক্ষার ব্রতে। তাঁর পরিবর্তিত জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাহিত্যকর্মেও পরিবর্তন এসেছিল। ‘হাজার চুরাশির মা’ বইটি ওই সময়েই লিখেছিলেন তিনি। উপন্যাসটা পড়লেও বোঝা যায়। ওই সময় দিনে চৌদ্দ-পনের ঘণ্টা কাজ করতেন মহাশ্বেতা দেবী। আদিবাসীদের মধ্যে কাজ শুরু করেন। তখন থেকেই তাঁর লেখা সমৃদ্ধ হতে শুরু করে। এভাবেই মহাশ্বেতা দেবী স্বপ্রকৃতিতে প্রবেশ করেন। তিনি ১৯৬৪ সালে বিজয়গড় কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন। সতেরো শ’ টাকা মাইনে পেতেন। তিনি নিজের লেখালেখির গুরুত্ব বুঝে শিক্ষকতার পেশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। আসলে লেখাই তাঁর জীবিকা ছিল। পরবর্তীকালে তিনি মূলত পশ্চিমবাংলার আদিবাসী এবং নারীদের ওপর কাজ করা শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে আদিবাসী, নিপীড়িত জনতা এবং নারীর উপর শোষণ, অত্যাচার, নিপীড়ন এবং বঞ্চনার কথা তুলে ধরেছেন। কথাশিল্পী মহাশ্বেতা দেবী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্পনীতির বিরুদ্ধে সরব ছিলেন। সরকার কর্তৃক বিপুল পরিমাণে কৃষিজমি অধিগ্রহণ এবং স্বল্পমূল্যে তা শিল্পপতিদের কাছে বিতরণের নীতির তিনি কড়া সমালোচক ছিলেন। এছাড়া তিনি শান্তিনিকেতনে প্রোমোটারি ব্যবসার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করেছেন। এছাড়াও বেশ কিছু সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে বিজ্ঞজনদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম সারিতে। মহাশ্বেতা দেবী বাংলা সাহিত্য-অঙ্গনে বহুমাত্রিকতা ও দেশজ আখ্যানের অনুসন্ধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। শুধুমাত্র উপমহাদেশেই নয়, বিশ্বের নানা দেশে তাঁর সাহিত্যকর্ম পঠিত ও আলোচিত হয়। তাঁর সাহিত্যকর্ম ইংরেজি, জার্মান, জাপানি, ফরাসি এবং ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। এছাড়া অনেকগুলো বই ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে: হিন্দি, অসমীয়া, তেলুগু, গুজরাতী, মারাঠী, মালয়মি, পাঞ্জাবি, ওড়িয়া এবং আদিবাসী হো ভাষায়। ১৯৭৯ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান ‘অরণ্যের অধিকার’ উপন্যাসটির জন্য। ভুবনমোহিনী দেবী পদক, নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য স্বর্ণপদক, ভারত সরকার কর্তৃক ‘পদ্মশ্রী’ পদক পান তিনি। এছাড়া জগত্তারিণী পুরস্কার, বিভূতিভূষণ স্মৃতি সংসদ পুরস্কার, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত লীলা পুরস্কারও লাভ করেন তিনি। ১৯৯৭ সালে ম্যাগসাসাই পুরস্কার পান আদিবাসীদের মাঝে কাজ করার জন্য। ১৯৯৮ সালে সাম্মানিক ডক্টরেট পান রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ভারতীয় ভাষা পরিষদ সম্মাননা ২০০১ অর্জনসহ আরও অনেক পুরস্কারে সম্মানিত হন বিশিষ্ট সংগ্রামী লেখক মহাশ্বেতা দেবী। ‘অরণ্যের অধিকার’ বইটির জন্য তিনি সাহিত্য আকাডেমি পুরস্কার পান। এই বইটি ভারতের মাওবাদীদের উপাখ্যান নিয়ে রচিত একটি উপন্যাস। মাওবাদীদের জীবনচরিত পাওয়া যায় এই বইটিতে। যে বইটি প্রত্যেক লড়াকু, বিপ্লবী, দেশপ্রেমিকদের পড়া উচিত। একজন সংগ্রামীকে একটি বই-ই বিপ্লবীপথে প্রলুব্ধ করতে পারে বলে মনে করি। সাহিত্যজগতে সেই ছোঁয়াই রেখেছেন বিশিষ্ট লেখক মহাশ্বেতা দেবী। তেমনিই আর একটি বই ‘বীরসা মুণ্ডা’। আদিবাসীদের জীবন-কর্ম নিয়ে বইটি রচিত। সহজ, সাবলীল বইটি পাঠ করা আবশ্যক। এই লড়াকু মানুষটি এত এত পুরস্কার লাভ করেছেন নিজের লেখনীর যোগ্যতার শক্তিতে। আমরা ইতিহাস অনুসন্ধান করলে জানতে পারি, নোবেল পুরস্কার লাভের সম্ভাব্য তালিকায় নাম ওঠার কথা। তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান লেখক এবং সংস্কৃতি ও মানবাধিকার কর্মী ছিলেন। যিনি নিজেকে কর্মী বলেই পরিচয় দিতে ভালোবাসতেন। নিজের বাস্তবজ্ঞান উপলব্ধি করতেন এবং সেই জ্ঞান লেখনীতেই লিখে গিয়েছেন। ইতিহাস ও রাজনীতির ভূমি থেকে যে-সাহিত্য রচনা শুরু করেন, তা কেবল শোষিত, লাঞ্ছিত ও বঞ্চিতের আখ্যান নয় একজন স্বদেশীয় প্রতিবাদী চরিত্রের সন্নিবেশও। মাটি ও মানুষ নিয়েই তিনি আজীবন লিখেছেন। প্রতিবাদী মধ্যবিত্ত প্রান্তিক ও পাহাড়ি-বনাঞ্চলের জীবন ও যুদ্ধ, নৃগোষ্ঠীর স্বাদেশিক বীরগাঁথা আখ্যান রচনার পারদর্শিতা তাঁকে বিশিষ্ট করেছে। ইতিহাস তাঁর সাহিত্যজীবনে সব সময়ই প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি মনেই করতেন ইতিহাসের ভেতর থেকেই বের হয়ে আসে সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং তার আনুষঙ্গিক লোকাচার, সমাজসংস্কৃতি, লোকজনসংস্কৃতি ও লোকায়ত জীবনপ্রয়াস। তিনি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় খুদাবক্স ও মোতির প্রেমের কাহিনী নিয়ে ১৯৫৬ সালে ‘নটী’ উপন্যাসটি লিখেছিলেন। যে উপন্যাসটি মানুষের জীবনচরিতের সাথেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি লোকায়ত নৃত্য-সঙ্গীতশিল্পীদের নিয়ে লিখেছিলেন মধুরে মধুর (১৯৫৮), সার্কাসের শিল্পীদের বৈচিত্র্যময় জীবন নিয়ে লিখেছিলেন ‘প্রেমতারা’ (১৯৫৯)। এছাড়াও যমুনা কী তীর (১৯৫৮), তিমির লগন (১৯৫৯), রূপরাখা (১৯৬০), বায়োস্কোপের বাক্স (১৯৬৪) প্রভৃতি উপন্যাস। মহাশ্বেতা দেবী রাজনীতি ও ইতিহাসের বিমিশ্রণে যেমন তুলে আনেন ঝাঁসির রানীর বীরত্বব্যঞ্জক স্বাধীনতা-সংগ্রামের চিত্র তেমনি মধ্যবিত্তের দ্বন্দ্বময় জীবনভাষ্য। এসব ভাবধারায় উল্লেখযোগ্য উপন্যাস-মধুরে মধুর (১৯৫৮), আঁধারমানিক (১৯৬৬, হাজার চুরাশির মা (১৯৭৪), অক্লান্ত কৌরব (১৯৮২), মার্ডারারের মা (১৯৯২) প্রভৃতি। তিনি প্রান্তিক আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস রচনা করে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত করেছিলেন। যেমন: কবি বন্দ্যঘটি গাঞির জীবন ও মৃত্যু (১৯৬৭), অরণ্যের অধিকার (১৯৭৫), চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর (১৯৮০), বিরসা মুণ্ডা (১৯৮১), টেরোড্যাকটিল, পূরণসহায় ও পিরথা (১৯৮৭), সুরজ গাগরাই (১৯৮৩), বন্দোবস্তি (১৯৮৯), ক্ষুধা (১৯৯২) এবং কৈবর্ত খণ্ড (১৯৯৪)। মহাশ্বেতা দেবীর নেওয়া একটি সাক্ষাৎকার পড়েছিলাম- বেশ কয়েকদিন আগে। সাক্ষাৎকার নিতে যে ভদ্রলোকটি তাঁর বাড়িতে যাবেন, তিনি পথ হারিয়ে ফেলছেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কে দিকনির্দেশনা দেবেন ভাবতে ভাবতেই তার চোখে পড়ে, একটা লন্ড্রি। যেখানে উনুনে কয়লা দিচ্ছিল এক রংচটা গরিব ঘরের মেয়ে। তাকেই জিজ্ঞেস করেন, মহাশ্বেতা দেবীর বাড়ি চিনো? মেয়েটি বেশ উৎসাহ নিয়ে বলেন, ‘মহাশ্বেতা দেবীর বাড়ি খুঁজছেন, বলবেন তো!’ তখন ওই মানুষটি খুব অবাক হয়ে ভাবছিলেন- মহাশ্বেতা দেবী কোনো ফিল্মস্টারও নন, ক্রিকেট খেলোয়াড় নন, রাজনীতি ব্যবসায়ী নন। একটি সামান্য তুচ্ছ মেয়ে তাঁকে চিনল কী করে? পরে একজন রিকশাওয়ালাও বলেছিলেন, এখানে যাকেই জিজ্ঞেস করবেন সেই বলে দেবে মহাশ্বেতা দেবীর বাড়ি কোথায়। এটার কারণ নিশ্চয়ই, লেখক হওয়া নয়। কেননা, সমাজে লেখকদের বাড়ি রাস্তায় কেউ বলে দিতে পারে না। এটার একমাত্র কারণ ছিল- মানুষটি ওদেরই মানুষ, ওই রংচটা পোষাকী গরিব মানুষদের মধ্যেই যাঁর বসবাস ছিল। যাদের জীবন-দর্শনই তাঁর লেখনীতে ফুটে ওঠেছে। এই উদাহরণটি এইজন্যই টেনেছি যে, একজন লেখকেরও কত কাজ থাকে, কতটা আপন হতে পারে সাধারণ মানুষের! একজন মানুষের জীবনে এর চেয়ে বড় সার্থকতা আর কীই বা হতে পারে? মহাশ্বেতা দেবী বলতেন, ‘আমি যা শিখেছি, জেনেছি তাই লেখার মধ্যে ব্যবহারের চেষ্টা করেছি। সেখানে কেউ বুঝতে না পারলে আমার কিছু করার নেই। আমি যা পারি তাই লিখেছি, লিখে যাচ্ছি। আমি আমার মতোই জীবনযাপন করেছি। কাজও করেছি- কোনো সমস্যা হয় নি। জীবনে কোনোদিন কৃত্রিমতার আশ্রয় নেই নি। এটা আমার বোধের উপলব্ধি।’ এই কথাগুলো কোড করার একমাত্র কারণ হলো- একজন মানুষ কতটা নিভৃতচারী হলে নিজের জীবনকে এভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন? যাঁর জীবনাদর্শনই ছিল শিশুসুলভ। যে জীবনে কোনো ধরনের হিংসে, কুটিলতা, অমানবিকতার আশ্রয় ছিল না। সমাজের নিপীড়িত জাতিগোষ্ঠির জন্য যতটুকু পেরেছেন কাজ করেছেন তিনি। সিঙ্গুরের কৃষিজমি যখন শিল্পপ্রতিষ্ঠায় সরকার নিয়ে নিচ্ছিল সেখানেও কাজ করেছিলেন, গুজরাটে যখন দাঙ্গা হলো তখনও বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি। মানুষকে সচেতন করা, মনুষ্যত্ববোধ জাগানোই যাঁর কাজ ছিল। সেটা লেখনীর মধ্যদিয়েই হোক, সাহস দিয়েই হোক, পাশে থেকেই হোক। তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজের মানুষ একসময় সকল অন্যায়, অবিচার, বৈষম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। যতই নিপীড়ন, নির্যাতন, বৈষম্য আসুক তারা তাদের অধিকার কেড়ে নিবেই। এই মহান বিশ্বাস থেকেই তিনি মেহনতি মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি মনে করতেন, সমাজের সকল অন্যায়, অবিচার, বৈষম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো উচিত লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের। সমাজের মানুষের কাছে নিজেদেরও দায়বদ্ধতা আছে। সবার এটা থাকা উচিত। কথাশিল্পী মহাশ্বেতা দেবী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও হাসান আজিজুল হকের লেখা পড়তেন। তাঁদের লেখনী তাঁকে গভীরভাবে প্রলুব্ধ করেছিল। তিনি বলতেন, ‘জীবনে বহুত লেখকের বই পড়েছি। বই ছাড়া আমার আর কি বিষয় হতে পারে?’ মহাশ্বেতা দেবী রবীন্দ্রনাথকে খুব কাছ দেখেছেন- শান্তিনিকেতনে পড়াশুনাকালীন সময়ে। সেসময়ই তিনি রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা, তাসের দেশ পড়েন। রবীন্দ্রনাথই তাঁকে লেখক জীবনে প্রভাবিত করেন। তিনি একবার এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘রবীন্দ্রনাথ শুধু আমার লেখক জীবনকে প্রভাবিত করেন নি, তাঁকে তো আমি মনের মধ্যেই বহন করে নিয়েছি।’ ঝাঁসির রানীর জীবন লিখবেন বলে জিদ করেছিলেন তিনি। তখন তাঁর ছেলেটি খুবই ছোট ছিলেন। ওকে রেখেই পড়াশুনার কাজ করতেন একনিষ্ঠচিত্তে। ঝাঁসির রাণীর বই করবেন বলে- ঝাঁসির গোয়ালিয়রে যান তিনি। ঘুরে ঘুরে দেখেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁসির রাণীর অবদান, ইতিহাসের দলিল-দস্তাবেজ, বিবিধ রেকর্ডপত্র যা পাওয়া যায় তাই তিনি সংগ্রহ করেন। ঝাঁসির রাণীর বংশের যারা বেঁচে ছিলেন তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন তিনি। তিনি মনেই করতেন, একজন লেখককে চরিত্র নির্ধারণ করতে হবে সমাজের বাস্তবতার নিরিখে। মহাশ্বেতার দেবীর গ্রন্থ তালিকা অরণ্যের অধিকার, নৈঋতে মেঘ, অগ্নিগর্ভ, গণেশ মহিমা, হাজার চুরাশির মা, চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর, শালগিরার ডাকে, নীলছবি (১৯৮৬, অধুনা ঢাকা), বন্দোবস্তী, আই.পি.সি ৩৭৫, সাম্প্রতিক, প্রতি চুয়ান্ন মিনিটে, মুখ, কৃষ্ণা দ্বাদশী, ৬ই ডিসেম্বরের পর, বেনে বৌ, মিলুর জন্য, ঘোরানো সিঁড়ি, স্তনদায়িনী, লায়লী আশমানের আয়না, আঁধার মানিক, যাবজ্জীবন, শিকার পর্ব, অগ্নিগর্ভ, ব্রেস্ট গিভার, ডাস্ট অন দ্য রোড, আওয়ার নন- ভেজ কাউ, বাসাই টুডু, তিতুমীর, রুদালী, উনত্রিশ নম্বর ধারার আসামী, মিলুর জন্য, প্রস্তানপর্ব, সিধু কানুর ডাকে, ব্যাধখণ্ডসহ ইত্যাদি বইয়ের প্রণেতা তিনি। উপমহাদেশের এই বিশিষ্ট লেখক ও কথাসাহিত্যিক ২৮ জুলাই ২০১৬ সালে ৯০ বছর বয়সে, কোলকাতার বেসরকারি হাসপাতাল বেলভিউতে দৈহিকভাবে মারা যান। ফুসফুসে সংক্রমণ নিয়ে দীর্ঘদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন অনিয়ন্ত্রিত ডায়বেটিসের কারণে দুটি কিডনিই নষ্ট হয়ে যায়। ফুসফুসের কাজও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনি বেঁচে থাকবেন যতদিন মানবসভ্যতা টিকে থাকবে- তাঁর কর্ম ও স্মৃতির মধ্যে। তাঁর কর্ম ও স্মৃতির প্রতি সংগ্রামী অভিবাদন। জয়তু মহাশ্বেতা দেবী। লেখক: লেখক ও অ্যাক্টিভিস্ট